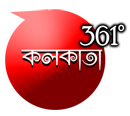ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ক আলোচনায় যার নাম প্রথমেই উচ্চারিত হয় সেই হীরালাল সেনের কোনও ছবিই পাওয়া যায় না। পাশাপাশি অনাদিনাথ বসুরও অর্ধেক ছবি নেই।তার মানে ১৯৩০ সালের আগে বাংলা চলচ্চিত্রের যেসব কাজ হয়েছিল সেকথা জোর দিয়ে বলার মতো কোনও প্রমাণ আমাদের হাতের নেই।সুখের কথা ১৯১৯ সালে তৈরি করা ম্যাডানদের ছবি ‘বিল্বমঙ্গল’ সম্প্রতি উদ্ধার করা গিয়েছে। এই ভূমিকার অবতারণা মৃণাল সেনের সিনেমা নিয়ে ভাবনাচিন্তার কারণে। যে মৃণাল সেনকে নিয়ে আমাদের আবেগের অন্ত নেই, যার সিনেমা আলচনায় আমরা এ কথাই বলে থাকি যে, তিনি ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়ের মতো বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্ব সংস্কৃতির পরিসরে বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সেই মৃণাল সেনের একাধিক ছবি হারিয়ে গিয়েছে।
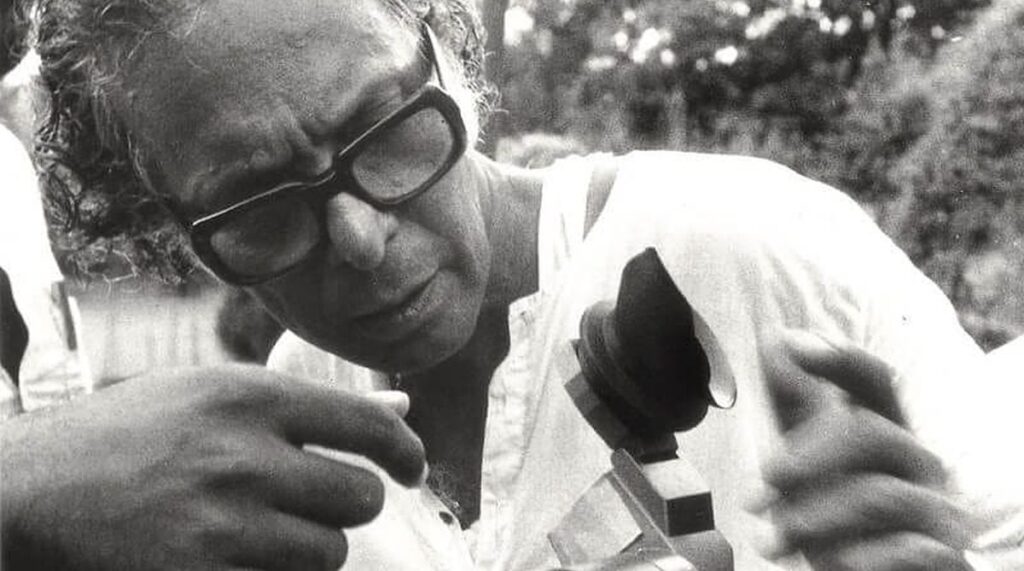
এই ঘটনা এমনই মর্মান্তিক যে স্বয়ং মৃণাল সেন নিজেই তাঁর একাধিক ছবির কপি কেনার জন্য সক্রিয় হয়েছিলেন। এই ছবিগুলি তাঁর প্রথমদিকে অর্থাৎ ষাট দশকে নির্মিত। যার মধ্যে মৃণাল সেনের তিনটি ছবি আছে যার কোনও চিহ্নই আজকে বাঙালি খুঁজে পাবেন না। অথচ সেই ছবিগুলি বাঙালির মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার একটা আয়না। ষাট দশকের বাঙালি কীভাবে বেঁচে ছিল সেকথা এই ছবিগুলিতে মৃণাল সেন বলেছিলেন। যেমন ‘পুনশ্চ’। এই ছবিটি ১৯৬১ সালে তৈরি করেছিলেন। ওই বছরই ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। ‘পুনশ্চ’-তে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। ছবিটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু সেই ছবির প্রিন্ট অনেক চেষ্টা করেও মৃণাল সেন খুঁজে পাননি। আরও মজার কথা মৃণাল সেনের ছবি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সব সময়েই ‘রাত ভোর’ ছবিটির কথা উল্লেখ করি। তারপরে ‘নীল আকাশের নীচে’ এবং সরাসরি ‘আকাশ কুসুম’ ছবির প্রসঙ্গে চলে যাই, কারণ আমাদের সংরক্ষণে ‘পুনশ্চ’ ছবিটি নেই। অথচ ওই ষাট দশকের গোড়ায় বাংলায় যে নায়িকা প্রধান চলচ্চিত্রের শুরু হয়েছিল, ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতা, ‘মহানগর’-এর আরতর সঙ্গে ‘পুনশ্চ’-এর বাসন্তীর উল্লেখ করাই যায়। ১৯৬১ থেকে ২০২৪- মাঝখানে এতগুলি বছর চলে গিয়েছে, বঙ্গ জীবনে কত কিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ‘পুনশ্চ’-র মতো একটি ছবির প্রাসঙ্গিকতা বঙ্গজীবনে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলে এই বাস্তবতাকে আমারা কোন দিক থেকে দেখবো- একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের অনন্ত দূরদর্শিতা, নাকি বঙ্গসমাজের অঙ্গ হিসাবে আমাদের নিতান্ত ব্যর্থতা?
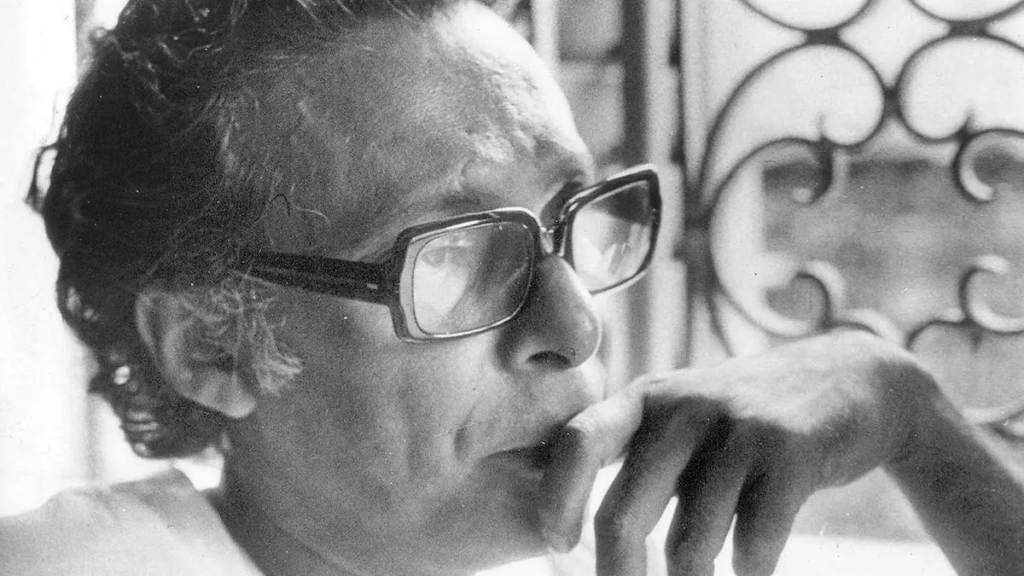
কেবলমাত্র ‘পুনশ্চ’-র চিহ্ন নেই তাতো নয়, তার পরের ছবি ‘অবশেষে’, যা ১৯৬৩ সালে নির্মিত, সেই ছবিটিরও খোঁজ নেই। ‘অবশেষে’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, সুলতা চৌধুরী, পাহাড়ি সান্যাল, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত প্রমুখ। ‘অবশেষে’-ও এক সাধারণ গল্পনির্ভর ছবি। কিন্তু ছবির বহু জায়গায় যথেষ্ট মোচড় আছে। আইনের দুনিয়ার মধ্যে যে মানুষের মনকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না, এ ছবির কাহিনি ও নির্মাণে সেই কথা উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে। কিন্তু বলা হয়েছে একটি নিটোল গল্পের মধ্যে দিয়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘স্বভাবের স্বাদ’ গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। প্রণব রায়ের গানের কথায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এই ছবিতে চারটি গান ছিল “স্বপ্নে ভরা এই বাদলবেলা…”, “দিনগুলি মোর ফুলের মতো…”, “আমার সকল চাওয়া বিফল হল…” ও “এই আকাশ এই হাওয়া এই আলো…”। গানগুলি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃণাল সেনের হারিয়ে যাওয়া ছবিগুলির মধ্যে আরেকটি হল ‘প্রতিনিধি’। ১৯৬৪-তে পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে এই ছবিটি তৈরি করেন মৃণাল সেন। মেয়েদের সামাজিক ভয় ভীতি ভেঙে বেরিয়ে আসার ডাক রয়েছে এখানে।
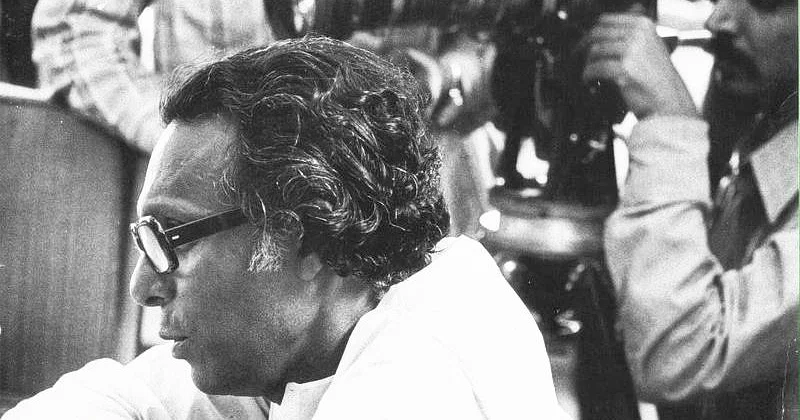
মৃণাল সেনের ছেলে কুণাল সেনের থেকে জানা গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে তাঁর বাবার “পদাতিক”, “খারিজ”, “কলকাতা ৭১” ছবির পাণ্ডুলিপি। শুধু পাণ্ডুলিপি নয়, বেলতলা রোডে ছোট্ট বাড়িতে একসময় ছিল প্রচুর বইয়ের সমারোহ। সেই সব বইয়ের অধিকাংশের খোঁজ মিলছে না। খোঁজ মিলছে না বহু পদক আর পুরস্কারের। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি, পদক ও পুরস্কার নাকি মৃণাল সেন একদিন পৌরসভার জঞ্জাল ফেলার গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন। কুণাল সেন এ বিষয়ে আরও বলেন, ২০০৩ সালের গোড়ার দিকে বেলতলার বাড়ি বদলের সময় হঠাৎ তাঁর বাবা সব কাগজ গোছাতে শুরু করেন। স্ত্রী গীতা সেনকে নিয়ে গোছগাছ শুরু করেন। বেশ কদিন গোছগাছও করেন। হঠাৎ একসময় মৃণাল সেনের মনে হয়, এসব রেখে আর কী হবে? তারপর পৌরসভার গাড়ি ডেকে তুলে দেন ওই সব কাগজ। ওই সময় গাড়ির চালক জঞ্জালে ফেলা তাঁর একটি ব্যাগ থেকে শুনতে পান ঝনঝনানির শব্দ। খুলে দেখেন তাতে কিছু মেডেল আর পুরস্কার। কিন্তু মৃণাল সেন গাড়ির চালককে বলেন, রেখে কী হবে? ফেলে দেন।’